মুসলিম সমাজ: অভিজাত শ্রেণি
তত্ত্বগতভাবে মুসলিম সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ জাতীয় বৈষম্য ছিল না। কিন্তু তাই বলে মুসলমান সমাজকে কঠোরভাবে শ্রেণিহীন সম্পর্ক দ্বারা চালিত—একথা বলা যাবে না। বংশ, অর্থ কৌলীন্য, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান মুসলমান জনসমষ্টির মধ্যে গভীর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে সম্রাট ও রাজপরিবারের পরেই ছিল অভিজাতদের স্থান। ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণিকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়—
-
(১) অহল-এ-সঈক্ (বা অহল-এ সামশির/অহল-এ-তীগহ) এবং
-
(২) অহল-এ-কলম।
‘অহল-এ-সঈফ্’রা ছিলেন সৈনিক বৃত্তিধারী উচ্চ রাজপুরুষ। ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাপর্বে এঁরাই দক্ষ ও সাহসী নেতৃত্ব দ্বারা রাজপুত প্রতিপক্ষের পরাস্ত করে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বভাবতই এঁদের সামরিক পদমর্যাদা সামাজিক স্তর নির্ণয়ে বিশেষ গুরুত্ব পেত। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ক্রম নিম্নস্তর হিসেবে খান, মালিক, আমির, সিপাহশালার ইত্যাদি অভিধা বিবেচিত হত। সাধারণভাবে সবাই ‘ওমরাহ’ (আমিরের বহুবচন) নামে পরিচিত হতেন। ওমরাহ ছিলেন সুলতানি শাসনের মেরুদণ্ডবিশেষ এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক ও রক্ষক। সামরিক ও অসামরিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পদে এঁদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। স্থানীয় প্রশাসক বা ইক্তাদার পদে নিযুক্ত বহু আমিরই প্রায় স্বাধীন কর্তৃত্ব ভোগ করতেন।
সুলতানি আমলে বিভিন্ন পদাধিকারী অভিজাতদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অভিজাতদের মধ্যে নানা বর্ণ ও ধর্মের বহিরাগত ও এদেশীয় ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। শাসকের বংশ পরিবর্তনের সাথে সাথে তৎকালীন রীতি অনুসারে অভিজাতের শ্রেণি চরিত্র বা সংখ্যায় পরিবর্তন আসত। সুলতানি শাসনের সূচনাপর্বে অভিজাতদের অধিকাংশই ছিলেন তুর্কিস্থানের মানুষ। তুর্ক বংশোদ্ভূত সৎ, সাহসী, দক্ষ ও নেতার প্রতি অনুগত ব্যক্তিরা এই পদে গ্রহণযোগ্যতা পেতেন। পরবর্তীকালে ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে আফগানরা অভিজাতর পদ-মর্যাদা পান। এঁরা হাসান আবদাল ও কাবুলের মধ্যবর্তী ‘রোহ’ অঞ্চলের অধিবাসী এবং মহম্মদ ঘোরীর বংশজাত বলে দাবি করতেন। মোঙ্গল আক্রমণের সূত্রে বহু পরাজিত মোঙ্গল সুলতানি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এঁরা নব-মুসলমান নামে পরিচিত ছিলেন। তবে সুলতানি শাসনব্যবস্থার সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় যোদ্ধাশ্রেণি রাজপুতদের সাথে তুর্কি সুলতানদের প্রাথমিক পর্বে বেশ শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ক্রমে রাজপুত নায়কদের অনেকেই সুলতানের বিশ্বাসভাজন হয়ে অভিজাতের মর্যাদায় ভূষিত হন। ক্রীতদাসত্ব থেকে সুলতানপদে উন্নীত শাসকের সাথে দাস অভিজাত বা স্বাধীন অভিজাতদের অহং-এর সংঘাত অভিজাতদের সামাজিক সম্পর্কের একটি অতি সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণে অভিজাতরা যেমন সুলতানকে মদত জোগাতেন, তেমনি কখনো কখনো সুলতানের কাজে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতেন। এমনকি সুলতান দুর্বল হলে নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নিতেও দ্বিধা করতেন না। কোনো কারণে একজন অভিজাত ক্ষমতা ও মর্যাদার আসন থেকে বিতাড়িত না হলে, আভিজাত্যের শিরোপা তার অধস্তন পুরুষেরাও লাভ করত। তবে একজন অভিজাত-সন্তান প্রথমে সুলতান বা অন্য কোনো অভিজাত ব্যক্তির পোষ্য বা কর্মী হিসেবে জীবন শুরু করত এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অর্জিত সরকারি পদের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারত। আভিজাত্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালে একজন অভিজাত ‘খান’ উপাধি পেতেন। এর নীচে ছিল। যথাক্রমে ‘মালিক’ ও ‘আমির’ খেতাবধারীরা। অধ্যাপক আশরাফ দেখিয়েছেন যে, দিল্লির সুলতানদের দরবারে অভিজাতশ্রেণির জন্য আমিরের নীচে কোনো খেতার ছিল না। সাধারণভাবে সকল শ্রেণির অভিজাতই প্রভূত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। নিজ নিজ গণ্ডিতে সকল অভিজাতই নিজেদের এক একজন সুলতান বলেই ভাবতেন। কেবল প্রকাশ্যে চলাফেরা বা দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় তাদের জন্য কিছু পৃথক আদবকায়দা মানতে হত।
সুলতানি যুগে উলেমাশ্রেণি :
মুসলিম সুবিধাভোগীশ্রেণির অপর অংশ ছিল ‘অহল-এ-কলম’ (men to pen) অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীশ্রেণি। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ্, জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত প্রমুখ ‘অহল-এ-কলম’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে এঁরা ‘উলেমা’ (একবচনে আলিম’) নামে পরিচিত হতেন। অভিজাত বা ওমরাহদের যদি সুলতানি শাসনের ‘শক্তি’ (Power) বলা হয়, তাহলে উলেমারা ছিলেন তার ‘বুদ্ধি’ (Brain)। ইসলাম ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উলেমা’র অবস্থান। এঁরা মুসলিম বুদ্ধিজীবিশ্রেণির প্রধান অংশরূপে বিবেচিত হন। আক্ষরিক অর্থে যাঁরা জ্ঞান (ইলম) অর্জন করেছেন তাঁরাই ‘আলিম’, বহুবচনে ‘উলেমা’। বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এই গোষ্ঠী কোরানীয় ব্যাখ্যা (তফসির), মহম্মদের ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান (ইলম্-ই-হাদিস্), ধর্মীয় আইন (ফিকা), দর্শন (ইলম-ই-কালাম) ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবি শ্রেণি রূপে (অহল-ই-কলম) এঁরা মর্যাদা পান। যাকর-ই-মুদাব্বির লিখেছেন যে, ভগবদ্ধাক্য প্রচারক ও ধর্মের প্রবর্তকের পরের স্থানগুলি পান সজ্জন ব্যক্তিরা (সিদ্দিকি), শহীদরা (শহীদী) এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা (আলিম)। এঁদেরই একটি অংশ ধর্মজ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পবিত্র ও সংযমী জীবন যাপন করতেন এবং জাগতিক চাহিদা বা রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। এঁরা পরিচিত হন ‘উলেমা-ই-আখরৎ’ নামে। কিন্তু সুলতানি শাসনকালে এই বুদ্ধিজীবিদের প্রভাবশালী অংশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হন এবং বিচার, আইন, প্রশাসন, ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। শাসক পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রাসাদ বিপ্লবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে অভিজাতদের শ্রেণিভুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালান। এঁরা পরিচিত হন ‘উলেমা-ই-দুনিয়া’ নামে। আইন অনুসারে এঁরা কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণি ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবে এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটি ‘বিশেষ গোষ্ঠী’ হিসেবে সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কাজে কর্তৃত্ব করার ফলে কালক্রমে একটি ‘শ্রেণি’ রূপে পরিগণিত হতে থাকেন।
এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অ-তুর্কি আরবীয় ও পারসিক ধর্মতত্ত্ববিদ্ এবং গোঁড়া সুন্নি। সুলতানের প্রিয়পাত্র ও মুখ্য সহযোগী হিসেবে এঁরা ওমরাহদের সমান কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভোগ করতেন। কোরান, হাদিস, কালান ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্র, শরিয়তি আইনকানুন, আরবি ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে এঁদের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অধ্যয়ন করতে হত। উলেমাদের প্রধান কাজ হিসেবে পবিত্র কোরান সাধারণ মানুষকে ‘ধর্মপথে আকৃষ্ট করার’ কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও ধর্মবিশারদ উলেমাদের জন্য সামাজিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসন নির্দিষ্ট থাকলেও, অতিমানবিক কোনো অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু নিজ শ্রেণির সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে অন্যান্য সামাজিক শক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য এঁরা স্বকল্পিত নতুন নতুন ধর্মীয় বিধান প্রচার করতে থাকেন। যেমন হজরত মহম্মদের ভাষ্য হিসেবে প্রচার করা হয় ‘উলেমারা সত্যদ্রষ্টাদের সার্থক উত্তরসাধক, তাই তাদের সম্মান দেখাও। এদের শ্রদ্ধা করলেই আল্লাহকে ভক্তি করা হয়’ কিংবা “শাস্ত্রবিধির শিক্ষক, শাস্ত্রবিধির ছাত্র, নিদেনপক্ষে শাস্ত্রবিধি ব্যাখ্যাকারের ধৈর্যশীল শ্রোতা—এই তিনটির যে-কোনো একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হতে ভুলো না। যারা এই তিন দলের সদস্য নয়, তাদের জন্যে ‘দোজখ নাজেল’ অনিবার্য ইত্যাদি।
ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের বিকাশের ধারায় উলেমারা প্রত্যাশিতভাবে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় অনুমোদন ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে ভারতে সুলতানি শাসনকে স্থায়ী ভিত্তি দিতে আগ্রহী সুলতানেরা অনেকেই রাজনীতির ওপর উলেমাশ্রেণির খবরদারি মেনে নেন। ভারতে সুলতানি শাসন আক্ষরিক অর্থে ধর্মাশ্রয়ী ছিল না। কিন্তু খলিফার অনুমোদন অর্জন দ্বারা নিজ কর্তৃত্বকে আইনের স্বীকৃতি প্রদানের ইচ্ছা অধিকাংশ সুলতানেরই ছিল। এমতাবস্থায় রাজনীতির ওপর উলেমাদের প্রভাব অনিবার্যভাবেই বেড়েছিল। প্রধান সদর, প্রধান কাজি প্রভৃতি ধর্মীয় ও বিচারবিভাগীয় পদে উলেমাদের নিযুক্তি সেই ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব করেছিল। ইলতুৎমিস, বলবন প্রমুখ নানাভাবে উলেমাদের সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করতেন। আলাউদ্দিন খলজি তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হলে উলেমাদের গোঁড়া মানসিকতা বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ করতেন না।
বাস্তবে কোরান-নির্দিষ্ট কর্তব্য এবং উলেমাশ্রেণির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। ড. আশরাফের ভাষায়: “উলেমার মুসলিম সম্প্রদায়কে নৈতিক সদ্গুণ ও ধর্মানুরাগের পথে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার মহৎ দায়িত্ব ত্যাগ করে বসেছিলেন।” সুলতান বলবন, বুগরা খাঁ, মহম্মদ-বিন্ তুঘলক প্রমুখ অনেকেই উলেমাশ্রেণির নৈতিক অধঃপতনের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলবনের মতে, সমগ্র উলেমা সম্প্রদায় সত্যনিষ্ঠা ও সৎ সাহস থেকে বঞ্চিত ছিল। বুগরা খাঁ ব্যথিত চিত্তে বলেছিলেন, “এরা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরা অর্থগৃধু, প্রবঞ্চক, পরকালের চিন্তা করে না, ইহলোকই এদের আরাধ্য দেবতা।” আমির খসরু লিখেছেন যে, “আইনের (কোরানীয়) ব্যাখ্যাকার এই উলেমারা ইসলামীয় আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাপীড়ক সুলতানকে সমর্থন করাই ছিল উলেমাদের একমাত্র ধর্ম।” খসরু এমনও বলতে দ্বিধা করেননি যে, উলেমারা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রীতির জোরেই সাধারণের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নিতেন। কিন্তু মানসিক ও প্রকৃত গুণাবলি যদি সামাজিক সম্মানের মানদণ্ড হত, তাহলে “মোল্লার তুলনায় যে কোনো অ-যাজক সাধারণ মানুষের সম্মানলাভের অধিকার সহস্রগুণ বেশি ছিল।”
বস্তুত, সুবিধাভোগী ওমরাহ ও উলমাশ্রেণি নিজেদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য সদাসতর্ক ছিলেন। অ-মুসলমান কিংবা নিম্নবংশীয় মুসলমানরা যাতে ক্ষমতা ও মর্যাদার কেন্দ্রে উন্নীত হতে না পারে, সেজন্য সুবিধাভোগীশ্রেণি সর্বদা বংশকৌলীন্য ও মিথ্যা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের আবরণে নিজেদের আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করতেন। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থরক্ষার কাজে এই শ্রেণির ঐক্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু অভিজাতদের মধ্যেও জাতিগত ও বংশগত ভেদাভেদ ছিল প্রকট। স্বয়ং মহানবির রক্তের অধিকারী শেখ ও সৈয়দরা ছিলেন সমগ্র মুসলিম-সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরে ছিল তুর্কি দাসদের অবস্থান। পরবর্তী স্তরে ছিল হিন্দুস্তানি মুসলিম অভিজাতদের স্থান।
সুলতানি যুগে সাধারণ মুসলিম জনতা :
সুবিধাহীন মুসলিম জনতা (আওয়াম-ও-খাল্ফ) এবং সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। মুসলিম জনসাধারণ বলতে বোঝায় মূলত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এবং দাসরা। ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান সমাজে তথাকথিত মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। অবশ্য কোনো কোনো বৃত্তিধারীর মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণির কিছু কিছু উপাদান অস্পষ্টভাবে বর্তমান ছিল। সামরিক ও সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত নিম্নপর্যায়ের কিছু কর্মচারী, ইতাদার-সহ নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি ইজারা পেতেন এমন কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি এবং বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত কিছু মানুষকে মধ্যবিত্তশ্রেণির উপাদানের ধারকরূপে চিহ্নিত করা যায়। সংখ্যায় অতি অল্প হলেও কিছু মুসলমান বণিক ও ক্যারাভান পরিচালককেও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
সাধারণ মুসলমান জনতার অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত ও দরিদ্র। কারণ প্রধানত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল। এই কাজে দু-ভাবে তারা আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করেছিল। প্রথমত, হিন্দুধর্মের বর্ণভেদের কঠোরতা এবং সামাজিক শোষণ থেকে রেহাই পাওয়ার আশা এবং দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণির ধর্ম গ্রহণ করে সামাজিক সাম্য পাওয়ার পাশাপাশি সরকারি পদে নিয়োগে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার বাসনা। কিন্তু শিক্ষার অভাব এবং সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণে এই সকল ধর্মান্তরিত মুসলমানের পক্ষে বহিরাগত, শিক্ষিত ও উচ্চবংশীয় মুসলমানদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা আদৌ সম্ভব হয়নি। কালক্রমে এই শ্রেণির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতই তাদের উচ্চাশা বৃদ্ধি পায় এবং মামেলুক সুলতানদের উন্নাসিকতা তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে খলজি বিপ্লব-এর সময় এই সকল হিন্দুস্তানি মুসলমান তুর্কি-আধিপত্য বিনাশের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।
সুলতানি যুগে ক্রীতদাস-দাসী :
মুসলিম জনসাধারণের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস-দাসী। ভারতে মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই সামাজিকভাবে দাসপ্রথা চালু ছিল। তবে মুসলমান শাসনের সূচনা হলে এই ব্যবস্থা একটি বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রাচীন গ্রিসের মতোই ভারতেও দাসদাসীরা ছিল যে-কোনো রূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরা মালিকের সম্পত্তিবিশেষ, কায়িক শ্রমদানে বাধ্য এবং অতি নিকৃষ্টমানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। সুলতানদের অধীনে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষাধিক দাসদাসী থাকত। সম্ভ্রান্ত প্রতিটি মুসলিম পরিবারেও দাসদাসী রাখার রেওয়াজ ছিল। অধ্যাপক আশরাফ লিখেছেন যে, মুসলিম অভিজাত ব্যক্তির জীবন হয় ‘সংগ্রাম’ (বজম), অথবা ‘আমোদ-প্রমোদ (বজম)-এই দুয়ের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাই নিজের সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দাসদাসীর সংরক্ষণ অনিবার্য হয়েছিল। ক্রমে দাসদাসী সংরক্ষণ সামাজিক মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হয়।
বিশ্বের নানাদেশ থেকে ভারতে দাসদাসীদের আমদানি করা হত। যুদ্ধবন্দি বা উপঢৌকন হিসেবেও দাসদাসী পাওয়া যেত। ভারতীয় দাসদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু বলে অসমিয়াদের খ্যাতি ছিল। অন্দরমহলের (হারেম) কাজকর্মের জন্য খোজা দাস নিয়োগ করা হত। শিশু দাসদের নপুংসক করে খোজা করা হত। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে খোজাদের কেনাবেচা বেশি হত। অনেক সময় মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ‘খোজা’ আমদানি করা হত। সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। মালিকের প্রয়োজন অনুসারে এদের ভাড়া শ্রমিক, সৈনিক, উপঢৌকন ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রীতদাসী সংরক্ষণের রেওয়াজ তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল। এদের প্রধানত দু-ভাবে ব্যবহার করা হত—–(১) ঘর-গৃহস্থালির কর্মী হিসেবে এবং (২) মালিককে সঙ্গদান ও তাঁর চিত্তবিনোদনের যন্ত্র হিসেবে। এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা ছিল কিছুটা উন্নত। দাসী সংগ্রহের সাধারণ নীতি হিসেবে অধ্যাপক আশরাফ জনৈক মুঘল অভিজাতের একটি কৌতুক ভাষ্য তুলে ধরেছেন : “গৃহকর্মের জন্য খোরাসানী নারী ক্রয় করো, শিশু পরিচর্চার জন্য হিন্দু নারী, আমোদ প্রমোদে সঙ্গদানের জন্য পারস্যসুন্দরী ক্রয় করো, আর এই তিন শ্রেণির দাসীকে কঠোর শাসনে বশীভূত রাখার জন্য ঘরে এনো অঙ্কু নদীর ওপারের মেয়েকে” (“Buy a khurasani women for her work, a hindu woman for her capacity for nurshing children, a persian woman for the pleasure of her company, and a trans oxianian for thrashing her as a warning for the other three.”)
তত্ত্বগতভাবে সমভাবাপন্ন ইসলাম সমাজে একজন ক্রীতদাস ও একজন স্বাধীন মানুষের সম অধিকার ভোগ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে চিত্রটি ছিল ঠিক বিপরীত। একজন ক্রীতদাস প্রকৃত অর্থেই ছিল সুবিধাহীন এবং আধুনিক সর্বহারাশ্রেণির থেকেও সর্বহারা। একজন মালিক তার দাসকে বিক্রয়, দাস অথবা ভাড়াশ্রমিক— যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারত। যুদ্ধবন্দি দাসদাসীদের বাঁচার অধিকারটুকু দেওয়ার জন্যই বিজয়ী প্রভুকে ‘মানবতাবাদী ও উদার’ অভিধায় ভূষিত করা হত। তবে সুলতানের বা অতি-অভিজাত ব্যক্তির দাসরা তুলনামূলক ভাবে অধিক সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হত। এরা অনেক ক্ষেত্রেই দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পেত। তবে এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা ছিল সমুদ্রে জলকণার সাথে তুল্য।
সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যাপক দাসপ্রথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। এইচ. জে. নাইবুয়র তাঁর ‘স্লেভারী অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, কঠোর ও ব্যাপক দাসপ্রথা সামাজিক প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। যথাযথ শিক্ষা ও স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধনের অভাব দাসদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে তাদের একশ্রেণির কর্কশ জীবে পরিণত করত। অধ্যাপক আশরাফ মনে করেন, ভারতের ক্ষেত্রেও দাসপ্রথার এই নেতিবাচক প্রভাব ছিল। হয়তো মধ্যযুগীয় ভারতে এই অসুস্থতা প্রকট ছিল না, কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এটি যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই।
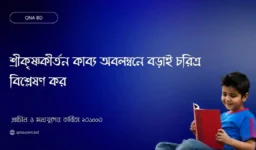
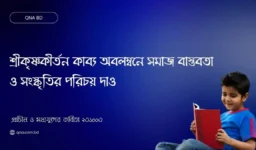
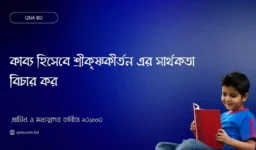
Leave a comment