অথবা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর
উত্তর : বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই কাব্যের প্রতিটি পদের প্রারম্ভে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বাকভঙ্গি এবং রচনাশৈলী এতে আপন স্বভাবে ভাস্বর। নিচে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:
১. প্রাকৃত অপভ্রংশ প্রভাবিত আনুনাসিক উচ্চারণ এবং বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে খুব বেশি হয়েছে যেমন- তোহ্ম, কাহ্নাঞি।
২. উচ্চারণে ই-কার এবং ঈ-কারের পার্থক্য রক্ষিত হয়নি যথা: ই> ঈ = তীন। ঈ > ই = সিতা।
৩. পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির এক যুগ্মস্বরে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বাংলা বাক্রীতির প্রভাব সূচিত করে। যেমন- বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন। (বংশীখণ্ড-২)
৪. ই-কার উ-কারে পরিণত হয়েছে। যথা: দুচারিণী > দ্বিচারিণী।
৫. আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের দরুণ ‘অ’ কার ‘আ’ কারে পরিণত হয়েছে। যথা: আতিশয়, আবল।
৬. বিপ্রকর্ষ, স্বরসংগতি, যুক্তবর্ণের একটি লোপ, স্বতো মূর্ধন্যীভবন ইত্যাদি আরো নানা ধ্বনিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যথা: বিপ্রকর্ষ – আরতি > আর্তি। স্বরসংগতি-রসন > রসনা।
যুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ -মধ্য > মাঝ।
স্বতো মূর্ধন্যীভবন – দক্ষিণ > ডাহিন।
পরিশেষে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষায় আমরা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি সুন্দর রূপের সাথে পরিচিত হই। পরবর্তীতে এর ভাব ও ভাষা বাংলা বাক্যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।
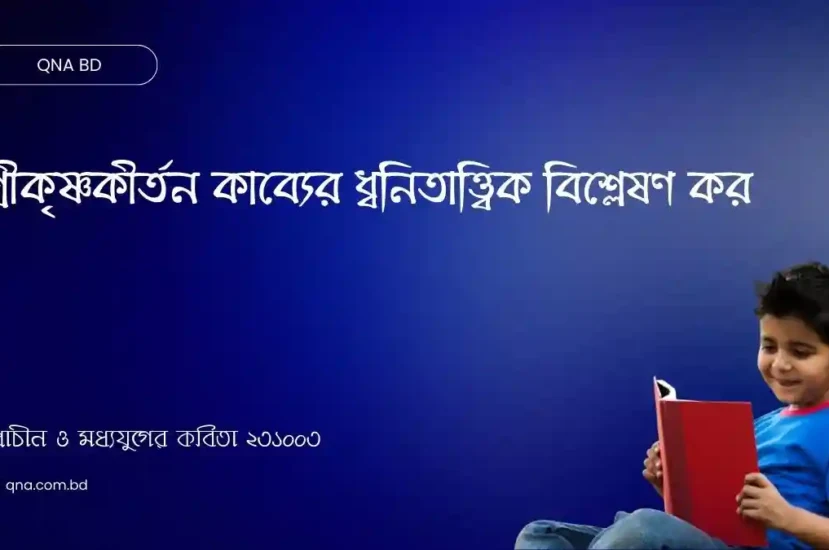



Leave a comment