আধুনিক বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র পরবর্তী কবি হিসাবে বিষ্ণু দে একটি আবশ্যিক নাম। আধুনিক বাংলা কাব্যের এলিয়ট তিনি। পরিচ্ছন্ন কাল জ্ঞান ও ইতিহাস চেতনাকে পৌরাণিক নানা অনুষঙ্গে জারিত করে কবিতাকে তিনি করে তুলেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন এক সময় প্রতিমা। রবীন্দ্রবৃত্তে অবস্থান করেও বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রকাব্যের মোহময় উজ্জ্বলতা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নতুন একটি আঙ্গিক দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে। প্রাচ্যের ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলা কাব্যে সাবলম্বের নিশ্চয়তা এনেছিলেন তিনি। রাবীন্দ্রিক কবিতার পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে উঠলেও শুধুমাত্র ব্যক্তি সর্বস্ব অনুভূতির চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি কবিত্বের শিখর স্পর্শ করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের বদলে বরং অনেক বেশি প্রমথ চৌধুরীকেই গ্রহণযোগ্য জেনেছেন। বিভিন্ন ভাস্কর ও চিত্রকরদেরও তিনি সমালোচনা করেছেন। আবার কবিতা রচনায় বিরোধী শিবিরের লোক হয়েও অপরিণত রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বিষ্ণু দে-র এই নতুন কাব্যাদর্শ ও কাব্যরুচি বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কাজেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রাবীন্দ্রিক কাব্যচেতনা, আঙ্গিক সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র কবিতাতেই। সমসাময়িক বিভিন্ন প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা এই বিষয়টিকে তাদের সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বিষয়ও করে তুলেছিল সেদিন।
চল্লিশের দশক শুরু হতে না হতেই গোটা বাংলা দেশ জুড়ে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নানা রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক হিসাবে বিষ্ণু দে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন আর ১৯৪৩-এর মন্বন্তর—এই দুই অভিজ্ঞতাকে এসময়ের কাব্য ‘সাত ভাই চম্পা’য় ফুটিয়ে তুলেছিলেন কবি। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস শেষ হতে না হতেই ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা-তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম কবি চেতনাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল। এ সময় থেকেই মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমান বিষ্ণু দে-র কবিতাকে বদলে দিতে শুরু করে। সমালোচক অরুণ সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “স্বাধীনতা উত্তর স্বদেশের মন্ত্রণা ও সম্ভাবনাকে তিনি বিষয় ও প্রকরণের অগাধ বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছেন। বিষ্ণু দে-র কাব্যপ্রতিভা চূড়ান্ত মাত্রা পেয়েছে ‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ (১৯৫৩) ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’ (১৯৫৮)। ‘আলেখ্য’ (১৯৫৮) এবং ‘স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ’ (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগুলির উল্লেখ যে কারণে এই আলোচনায় প্রয়োজনীয় সেটি হল। প্রায় প্রতিটি কাব্যেই বারবার চলে এসেছে রবীন্দ্র অনুষঙ্গ।
আপাত অর্থে রবীন্দ্র বিরোধী কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথকে ঐতিহ্য হিসাবেই রক্তে ধারণ করেছিলেন বিষ্ণু দে। জীবনের অপূর্ণতাজনিত বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কবি যতই অস্থির হয়ে উঠেছেন ততই দেখেছেন পূর্ণতার প্রতীক হয়ে ঐতিহ্য পরম্পরায়, সত্তার একমাত্র বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রবীন্দ্রনাথ’ কবিতা গুচ্ছের কবিতাগুলি বিষ্ণু দে সম্পর্কে এমন ভাবনার বোধকেই ছড়িয়ে দেয় আমাদের অন্তরে। রবীন্দ্রবিরোধিতার যে পরিমণ্ডলটি বাংলা কাব্য সম্পর্কে রোমান্টিকতার অর্থহীন ভাবাবেগের অভিযোগ তুলে এনেছিল, সে অভিযোগের উচ্চারক বিষ্ণু দে-ও ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের পর থেকে জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালাবদলের যে প্রবল ক্ষয়িষ্ণু প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন রোমান্টিকতা সর্বস্ব অর্থহীন ভাবালুতাই রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয় নয়।
‘রবীন্দ্রনাথ’ কবিতাগুচ্ছের কোথাও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেননি বিষ্ণু দে। কিন্তু কবিতাগুলির প্রতিটি পংক্তিই রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক অনতিক্রম্য বলিষ্ঠতা ও কর্মনিষ্ঠ চরিত্রের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সূর্যমুখী। রবীন্দ্রবিরোধীতার প্রবল আয়োজন যখন সমগ্র দেশজুড়ে বিস্তৃত হয়ে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে করলেন আত্মীকরণ। বুঝলেন এক হাতে বাঁশরী অন্যহাতে রণতুর্য নিয়েই তার যাত্রা। আবার রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের প্রবল সমারোহ, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন যখন ২৫শে বৈশাখের রাতেই অনেকখানি ম্লান হয়ে আসে তখনও বিষ্ণু দে বলতে ভোলেন না, ‘সভায় কাগজে বৃথা স্তোকস্তুতি অথবা গঞ্জনা’। বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন একটি ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণ নয়, জীবনযাপনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে রবীন্দ্রচেতনার সম্যক উপলব্ধি আমাদের অন্তরে জাগরূক রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সভ্যতার প্রবল দুর্দিনে আকাঙ্ক্ষার মেঘদূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নেমে আসবেন আমাদের সত্তায় এই কামনা করেছেন বিষ্ণু দে,
“রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রঙ”
যুগ ও জীবনের সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রেম সৌন্দর্যবোধ কিংবা তার আনন্দময় ধর্মের অপ্রাসঙ্গিকতা প্রথমে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও বিষ্ণু দে যখন দেখলেন রবীন্দ্র বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরে আসতে গিয়ে আধুনিক কবিরা এক প্রবল ‘না’-এর জগৎ গড়ে তুলছেন, তখন তিনি সচেতন ভাবেই সেই পথে হাঁটলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের বিপুল জ্ঞান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিকাশের দ্বান্দ্বিক ইতিহাস বোধ, মার্কসীয় জীবন চেতনায় বিশ্বাস বিষ্ণু দের কাব্যভুবনকে সম্পূর্ণ অন্য এক অভিব্যক্তি দিয়েছে। সমালোচকের কথায়, “আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জ থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসের ধ্রুবলোক।”এই বিশ্বাসকে অন্তরে চিরজাগ্রত রাখতে পেরেছিলেন বলেই যুগগত বিকার ও স্ববিরোধিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিষ্ণু দে। বিচিত্র প্রতিকূলতা ও দ্বন্দ্ব মুখরতার পথ কবির সামনে দেখা দিয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত সমাধানের পথকেই শেষ পর্যন্ত অন্বিষ্ট করে তুলেছিলেন বিষ্ণু দে। পঁচিশে বৈশাখের রবীন্দ্রস্মরণ পংক্তিমালা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—
“জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ব্যেপে
প্রতিটি ঊষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যত ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয় চৈতালী নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঠে।”
রাবীন্দ্রিক জীবনবোধের এই মন্ত্রেই বিষ্ণু দে জীবন-পিপাসাকে হারাননি। অথবা প্রেমের মাধুর্যকে জীবন থেকে নির্বাসিত করেননি। সেই বিশেষ জীবনধারাই প্রতীক বিষ্ণু দে’র ‘দামিনী’ কবিতা।
‘দামিনী’ কবিতাটি ১৯৬৩-তে প্রকাশিত ‘স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৬০-এর ১১ই জানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসটি পাঠ করে ‘দামিনী’ কবিতাটি রচনার ভাবনা বিষ্ণু দে-র মনে আসে। দামিনীর জীবনাকাঙ্ক্ষা, শ্রীবিলাসকে ভালোবেসে মৃত্যুময়তার পরপারে যে জীবন রয়েছে, সেখানে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণু দে-কে ভাবিয়ে তুলেছিল। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে দামিনীকে আমরা প্রথম দেখি লীলানন্দের আশ্রমে। সে বিধবা, কিন্তু জীবনের দাবীতে রক্ত মাংসের বাস্তবকে অস্বীকার নয় প্রবলভাবে স্বীকার করার শিক্ষাই সে পেয়েছিল। তাই লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমের শুষ্ক জীর্ণ আচার সর্বস্ব ভক্তিবাদকে সমস্ত অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারেনি সে। শচীশকে ভালোবেসেছিল দামিনী। কিন্তু প্রতিদানে শচীশের সামান্যতম স্বীকৃতিও সে পায়নি। লীলানন্দের শুষ্ক ভক্তিমদের ফোয়ারায় নিমগ্ন শচীশ চিরকাল মনে করে এসেছে নারী সাধনার পথের অন্তরায়। কঠিন প্রত্যাখ্যানে শচীশ এরপর গুহার অন্ধকারে দামিনীকে আঘাত করে। সেই আঘাত দামিনীর বুকে একটি স্থায়ী ক্ষত করে দিয়েছিল। এরপর দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করে। যদিও দামিনী জানে সমস্ত সত্তা দিয়ে শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু শ্রীবিলাসের ভালোবাসা প্রতিদানহীন। প্রেমের যে আঘাত শচীশের কাছ থেকে দামিনী পেয়েছিল সে শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলেছিল শ্রীবিলাস। প্রায় নিভে আসা জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দামিনীর বাঁচবার আকুলতা তখন কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।” আসলে শচীশের উপেক্ষা আর শ্রীবিলাসের প্রতিদানহীন ভালোবাসা গ্রহণ না করতে পারার যন্ত্রণাই দামিনীকে জীবন সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই পুনর্জন্ম চেয়েছে সে।
দামিনীর আকণ্ঠ এই জীবনতৃষ্ট্বা সঞ্চারিত হয়ে গেছে বিষ্ণু দে-র মনেও। দামিনী আর জীবনের পূর্ণতা যেন সমীকৃত হয়ে ধরা পড়েছে কবির হৃদয়ে। রবীন্দ্রনাথের দামিনীর আকাঙ্ক্ষা পরিণাম খুঁজে পেয়েছিল শ্রীবিলাসের প্রেমময় মুগ্ধতায় কিন্তু কবি বিষ্ণু দে সেই সীমাবদ্ধ পরিশীলিত প্রেমজগৎ থেকে সরে এসে দামিনীকেই পূর্ণতার প্রতীকের ব্যঞ্জনা দিতে চান। কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে দামিনী জীবন-পিপাসা আর কবির আকাঙ্ক্ষা যেন এক হয়ে যায়। কবিকে বলতে শুনি –
“আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি, দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে।”
রবীন্দ্র অনুভবকে চৈতন্যের গভীরে সঞ্চারিত করে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটে সত্য করে তুলতে চেয়েছেন কবি। শুধুমাত্র রবীন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রনাম নয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি হৃদয়ের অতৃপ্তির বোধকেও কবিতায় তুলে এনেছেন বিষ্ণু দে। কারণ তিনি অনুভব করেছেন, জীবনের প্রেমময় পূর্ণচন্দ্রের প্রতি প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে এক অসীম আকুলতা। আর জীবনের পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ পাওয়া যেতে পারে প্রেম ভালোবাসার নিমগ্নতাতেই। কবিতাটির প্রথমে তাই দামিনীর অন্বিষ্ট যে জীবনের পূর্ণচন্দ্র তারই ব্যাপ্ত রূপকে প্রতীকায়িত করেছেন কবি। দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্র উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্র দামিনীকে আশ্রয় করে কবিও পৌঁছাতে চেয়েছেন প্রেমের পূর্ণ স্বরূপে। আর তৃতীয় স্তবকে দেখিয়েছেন কবির প্রেমও ব্যক্তিতে সীমায়িত নয়, বহুব্যাপ্ত হয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজীবনের প্রাঙ্গণতলে।
সময়ের সঙ্কটে, সভ্যতার সঙ্কটে মানুষের প্রতি প্রোথিত আস্থা বিশ্বাস রবীন্দ্র জীবনভাবনার মধ্যে দিয়ে শিকড়ের সন্ধানে ফিরেছেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণতার স্বরূপ হিসাবে এই আত্মীকরণ কিন্তু উপলক্ষ্যমাত্র নয়। সরাসরি তাকে অনুসরণ বা অনুকরণও নয় বিষ্ণু দে আসলে দেখাতে চেয়েছেন, আমরা তাঁর সৃষ্ট পরিপূর্ণতার জগৎ থেকে কতটা সরে এসেছি। পরিপূর্ণ রবীন্দ্রজগৎকে সামনে রেখে আজকের ক্ষষিষ্ণু পৃথিবীকে তিনি খুলে খুলে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানবতার অবক্ষয় অসম্মান, অর্ধগৃধু মানসিকতা, মার্কসবাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় ইতিহাস-পরম্পরা, মানব ঐতিহ্য সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে যামিনী রায়ের সঙ্গে পরিচয়ও রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষায় বিষ্ণু দে-র অন্যতম সংযোগের কারণ হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বিশেষ সাহিত্যিক আশ্রয়ভূমি। ফলে চল্লিশের দশকের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি সামনে রেখেও, সমস্ত যন্ত্রণার স্পর্শ বুকে চেপে রেখেও রবীন্দ্রপ্রণামের পূর্ণতায় সত্তার অবগাহন বিষ্ণু দে র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।
“…..মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,
অলখ সংগীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয়
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে।”
রবীন্দ্র উত্তরাধিকারকে সমস্ত মন-প্রাণ-সত্তা দিয়ে লালন করতে পেরেছিলেন বিষ্ণু দে। প্রাণের উন্মুক্ত গঙ্গায় বৈচিত্র্যের যে সহস্রধারা বহমান সময়ের দীর্ণতা তাকে আবিল করতে পারেনি কখনও।
“প্রাত্যহিক ফাল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দ ভৈরবী।”
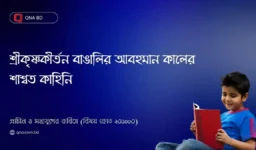
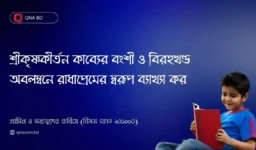
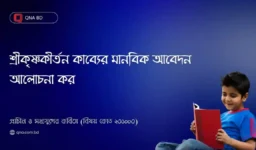
Leave a comment