“দুঃখ দৈন্যের ভাষাচিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব অসাধারণ হলেও সমগ্রভাবে মুকুন্দরাম দুঃখবাদের কবি নন।”- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের প্রথম খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটি বিচার করো।
দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কনে অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও দুঃখবাদ নয়, জীবনরসের উপভোগই মুকুন্দরামের স্বভাব ধর্ম। এই উক্তির সঙ্গতি বিচার করো।
বহুদর্শী প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সুকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে একটি অতিশয় মূল্যবান কথা বলেছেন যে সুকাব্য হবে ‘সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য’ অর্থাৎ এ কাব্য সংবেদনশীল চিত্তে রসের উদ্বোধন ঘটাবে। এ থেকে আমরা একাধিক সত্যে উপনীত হতে পারি—যিনি কাব্যনির্মাতা, তিনি হবেন রসিক পুরুষ, তিনি অপরের হৃদয়ে প্রবেশ ক’রে রসের ভাণ্ডারকে আত্মস্থ করতে পারবেন; কাব্য হাঁবে রস-যুক্ত কারণ কবির সরসতা তাতে হ’বে সঞ্চারিত এবং পাঠকও হবেন রসগ্রাহী—যিনি কাব্যপাঠে কবিচিত্তের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করবেন এবং তাঁর মনে জাগবে অনুকম্পার ভাব। এ অবস্থা হলেই কাব্য হয় সহৃদয়-সংবেদ্য। অতএব যিনি হ’বেন উৎকৃষ্ট কবি, তার চিত্ত হবে অতিশয় সংবেদনশীল— পরিবর্তনশীল জগতে নিত্যনিয়ত যে সকল ভাবধারার উত্থান-পতন ঘটেছে, কবি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্ত্রে সেগুলি জাগাবে সাড়া এবং কবি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাকে রূপান্তরিত ক’রে তুলবেন সাহিত্যের বুকে। আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই বুঝতে পারবো–কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে কেন দুঃখবোধ এত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দুঃখবোধের সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক যে অপরিহার্য নয়, সে কথাটাও এই সঙ্গে বুঝে নেওয়া দরকার।
কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী যে কালে এবং যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য প্রশ্নটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার একটু বিচার প্রয়োজন। কবি যখন জন্মভূমি ত্যাগ ক’রে যান তখন রাজা মানসিংহ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার দিল্লিতে তখন মুঘল বাদশা আকবর তক্তাসীন— সমগ্র সাম্রাজ্যে সুশাসন বিস্তারে সতত সচেতন এবং তারই এক অধস্তন কর্মচারী ডিহিদার মামুদ সরীফ এবং তার উজীর রায়জাদার অত্যাচারে সেলিমাবাজ পরগণার তাবৎ প্রজাকুল সদা-সন্ত্রস্ত। স্বেচ্ছায় সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যেতে চাইছে অনেকে, কবি সপরিবারে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আরড়ার ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের রাজসভায়— বাঁকুড়া রায় সম্ভবত একজন গ্রাম্য জমিদারই ছিলেন। অতএব, কবি মুকুন্দ যে সমাজ জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, তা’ ছিল এক গ্রাম্য সমাজ—যেখানে অধিকাংশ প্রজাই ছিল কৃষিজীবী এবং যাদের কোনকালেই – আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও পর্যাপ্ত ছিল না, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা কিংবা নাগরিকতাবোধের সঙ্গেও তাদের পরিচয় থাকার কথা নয়। কবিকঙ্কণের কল্পনার রাজ্য গুজরাট কিংবা কলিঙ্গের রাজসভায় যখন ‘কাঁচকলা’ ভেট নিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন বাস্তবের রাজা রঘুনাথ বা বাঁকুড়া রায়ের দরবারেও সম্ভবত এর অধিক রমরমা ছিল না। এত সব কথা বলার তাৎপর্য এই ব্যক্তিগত জীবনে কবি মুকুন্দ সম্ভবত সমৃদ্ধিমান সমাজের সঙ্গে বেশি পরিচিত ছিলেন না, তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতি দারিদ্র্যবিড়ম্বিত গ্রামীণ সমাজেই গন্ডীবদ্ধ ছিল। অভাবগ্রস্ত দুঃখময় জীবনকে তিনি যতটা কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার বিপরীত চিত্রের সঙ্গে তেমন পরিচয়ের সুযোগ তার ঘটে ওঠেনি। এই কারণেই কবিকঙ্কণের কাবো দুঃখ, অভাব, দারিদ্র্যের ছবি যতটা বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য হ’য়ে উঠেছে, সুখস্বচ্ছলতার ছবিতে তেমনটি কখনো হয়ে উঠতে পারে নি, তাকে অনেকটা কৃত্রিম বলেই বোধ হয়।
চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বপ্নাদেশেই হোক্ অথবা পৃষ্ঠপোষক রাজার অনুরোধেই হোক, কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচনা করলেন ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’—যাতে আছে ব্যাসন্তান কালকেতুর কাহিনী। গ্রামের প্রান্তে (‘কিরাতনগরে বসি’) বনের উপাস্তে বাস করে কালকেতু হঠাৎ করে দেবী চণ্ডীকার কৃপায় প্রচুর পরিমাণ দৈবধন লাভ ক’রে গুজরাট বন কেটে নগর পক্তন ক’রে তার রাজা হয়ে বসে কালকেতু। এই কাহিনীটি পূর্বাগত এবং ঐতিহ্যবাহী – কাজেই কাহিনীকে নতুন কোনো রূপ দেওয়া কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তবে নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনার প্রয়াস কিছুটা ছিলই। মুকুন্দও সেই সুযোগ গ্রহণ ক’রে রচনা করলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কবির কল্পনা আকাশ ছুঁতে পারে, তবে সার্থক কবি তার কল্পনাকে বাস্তবের ধার ধরেই চালিয়ে থাকেন। তাই কবিকুল-চূড়ামণি মুকুন্দও কখনই কল্পনার লাগাম আলগা করে দেননি—বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই ফাঁক পূরণ করেছেন। তার ফলে, কাব্যে দুঃখের চিত্রগুলি বড় বাস্তব হ’য়ে উঠেছে এবং কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, কবি মুকুন্দ নিশ্চিতই দুঃখবাদী এবং সংশয়বাদী ছিলেন বলেই তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস এমন বাস্তব ভূমি পেয়েছে। সত্য বটে দুঃখের চিত্র অতিশয় বাস্তব এবং আন্তরিকতাপূর্ণ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন।
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুঃখের চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে—’গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’ – বর্ণনা প্রসঙ্গে ডিহিদারের দ্বারা অত্যাচারিত প্রজাদের কাহিনী বর্ণনায় ও ব্যক্তিগত কাহিনীতে— সেখানে কবি পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন কোনো এক অজানা মুলুকে, পথে দস্যুভয়, শ্রম, ক্লান্তি, তৈল বিনা, কৈলু স্নান করিলু উদক পান / শিশু কাঁদে ওদনের তরে।’ হরগৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনাতেও এক দারিদ্র্যপীড়িত দম্পতির অভাবজনিত কোন্দল ও গৃহত্যাগের কাহিনী; বনের পশুদের কাতর ক্রন্দনেও যেন অত্যাচারিত প্রজাকুলের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়; ফুল্লরার বারমাস্যায় অতিশয় দারিদ্র্য জর্জরিত এক গৃহবধূর হাহাকার; কলিঙ্গ রাজ্যে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে কৃষকদের দুঃখবেদনা প্রভৃতি উপকাহিনী ও ঘটনার বর্ণনায় আত্যন্তিক দুঃখদুর্দশার চিত্রগুলি এত বাস্তব হ’য়ে উঠেছে যে কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে এদের সম্পর্কের একটি যোগসূত্র: আবিষ্কার করতে লোভ জাগাবারই কথা। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাবে, কবি-স্বভাবের বশবর্তী হয়ে কবিকঙ্কণ এই যে দুঃখময় জীবনের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হ’য়ে উঠেছেন, তার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কিংবা বাস্তব জীবনবোধের কোনোই সম্পর্ক নেই বলেই কবিকে দুঃখবাদী কিংবা সংশয়বাদী – কিছুই বলা যায় না।
যিনি জীবনে দুঃখকেই একমাত্র সত্য বলে জানেন, দুঃখের পরে জীবনে আবার দুঃখ আসতে পারে, যার মনে বিশ্বাস নেই জগৎ দুঃখময় জীবন দুঃখময়, দুঃখ ছাড়া জগতে আর কোনো সত্য বস্তু নেই—সুখের চিত্র আমরা যা দেখতে পাই, তা মায়া মাত্র, বস্তুত সুখের কোনো অস্তিত্ব নেই—এমন প্রত্যয় যার মনে দৃঢ়মূল তাকেই বলা চলে দুঃখবাদী জাগতিক এবং বাস্তব সত্যেও এদের সংশয়, তাই এদেরই সংশয়বাদীরূপেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস–মুকুন্দ কবিতে এই দুঃখবাদ বা সংশয়বাদের কোনো অস্তিত্বই নেই।
এক একটি ক’রে কাহিনী বিশ্লেষণ ক’রে দেখা যাক্। প্রথমেই কবির আত্মজীবনীমূলক কাহিনী— এতে দু’টি পর্ব, এক পর্বে আছে ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজাদের কাহিনী, অপর পর্বে মুকুন্দের নিজস্ব উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী। প্রথম পর্বটি ঐতিহাসিক সত্যের একটি বর্ণনা কবির ব্যক্তিগত ভাবনা-কামনার কোনো প্রতিফলন পড়বার কোনো সুযোগই নেই। আর কবির ব্যক্তিগত কাহিনীতে যে পথকষ্টের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার স্থায়িত্ব মাত্র দু’দশ দিনের। এর পরই কবি আশ্রয় পেলেন যে ভূমাধিকারীর নিকট, সেখানে তার জীবন যে বেশ সুখে শান্তিতেই অতিবাহিত হয়েছিল, তার স্বীকৃতি রয়েছে কবির লেখাতেই—
‘রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আরড়া নগরে।’
কাজেই কবি মুকুন্দ সুখী জীবনই যাপন করেছেন, তার জীবন দর্শনে দুঃখবাদ বা সংশয়বাদের কোনো স্থান থাকার কথা নয়।
হরগৌরীর সংসার যাত্রায় কিছু অভাব-অনটনের, কিছু ঝগড়াঝাটির বিবরণ আছে। এখানে তিনি যে নগাধিরাজ হিমালয়ের সংসারচিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানেও অভাবের চিত্র সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কবি গ্রামজীবনের যে চিত্র নিজ পরিবারে অথবা চারিপাশে দেখেছেন, সেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্রকেই এখানেও রূপায়িত করেছেন। অভাব-অনটনের সংসারে ঝগড়াঝাটি থাকতেই পারে–কিন্তু একে দুঃখময় জীবনের ইতিহাস বলে চালানো যায় না। কৈলাসে শিবকে যেমন ভিখারি বেশে দেখা গেছে, তেমনি মা অন্নপূর্ণার ‘ভাঁড়েও মা ভবানী’-কেদেখা গেছে। এ থেকে কোনো কিছুই সিদ্ধাস্ত করা চলে না, কারণ একটু পরেই দেখা গেছে, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র শিবের পূজা করছেন এবং ভগবর্তী শুধু যে মর্ত্যলোকে পূজা পেয়েছেন তা নয়, তিনি ব্যাধসস্তান কালকেতুকেও রাজা হ’বার মতো ধন দান করেছেন, কাজেই এই সব দৈব ব্যাপারে দুঃখের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।
মুকুন্দ চক্রবর্তীর দুঃখবাদের সমর্থনে প্রধান যুক্তি উত্থাপিত হয় ‘ফুল্লরার বারমাস্যা’র উল্লেখে। এখানে নিম্নবিত্ত গৃহস্থজীবনের অভাব-অনটনের যে বাস্তব চিত্রপট উন্মোচিত হয়, তেমনি দৃষ্টান্ত সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে মুকুন্দের বাস্তব চিত্রাঙ্কন ক্ষমতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আর ফুল্লরা তার অভাবগ্রস্ত জীবনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার পিছনে রয়েছে তার ঈর্ষাকাতর মেয়েলি বুদ্ধি। তার আশঙ্কা হয়েছিল, ঐ ষোড়শী রমণী বুঝি তার স্বামী-প্রেমে ভাগ বসাতে চায়। এই অভাবের দুঃখকষ্টের চিত্র এঁকে ফুল্লরা তাকে সরাতেই চেষ্টা করেছিল। ফুল্লরার জীবনে আর্থিক অনটন ছিল, এটি বাস্তব সত্য, কিন্তু তার জীবনে যে কোন দুঃখ ছিল, তা’ কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। সে ছিল স্বামী প্রেমে গরবিনী, স্বামীর ওপর তার অসপত্য অধিকার অতএব তার মতো সুখী কে? যাতে অপর কেউ আর সুখে ভাগ বসাতে না পারে, তার জন্যই সে দুঃখের কাঁদুনি গেয়েছেন। ফুল্লরা খুব দুঃখের ভান ক’রে বলছে—
‘বড় অভাগ্য মনে গণি, অভাগা মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণি।।’
তার বক্তব্যের মূলকথাটি এই সর্পাঘাতে মৃত্যুই ছিল তার কাম্য। কিন্তু এটা যে প্রকৃতপক্ষে তার মনের কথা নয়, তা প্রমাণ করা অত্যন্ত সহজ। প্রকৃতই যদি তার জীবন দুঃসহ মনে হ’তো, তবে তো ফুল্লরা ঐ ষোড়শী রূপসীর হাতে স্বামীর ভার সঁপে দিয়ে আত্মোৎসর্গ করতে পারতো অথবা সুখের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তা না ক’রে সে যে তার অভাবগ্রস্ত দুঃখের সংসারকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফুল্লরার জীবনে অভাব থাকলেও দুঃখ ছিল না। পরবর্তীকালে কালকেতু-ফুল্লরার জীবনের অভাবই যে শুধু দূর হয়েছিল তা নয়, তারা রাজসিংহাসনেও অধিষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব এখানেও দুঃখবাদ কিংবা সংশয়বাদের কোনো অবকাশ নেই।
বন্য পশুদের দুঃখনিবেদন ও কাতর ফ্রন্দনের মধ্যে প্রকৃতই নির্যাতিত প্রজাকুলের হৃদয়বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুত ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাদের অবস্থাই পশুদের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও দুঃখকে চরম সত্য বলে গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে দেবী চণ্ডী তাদের অভয়দান ক’রে কালকেতুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন, অপরদিকে কালকেতু যখন নিজে রাজা হ’ল, তখন প্রজাদের এত সুযোগ-সুবিধে দিয়েছিল যে তাদের অভাব-অভিযোগ বলতে আর কিছুই ছিল না। অতএব এখানেও কবির দুঃখবাদী কিংবা সংশয়বাদী হবার কোনো সুযোগ নেই।
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ ক’রেই এভাবে দেখানো যায় যে কবি দুঃখময় জীবনের পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা সৃষ্টি করলেও, ওটিকেই চরম সত্য বলে মনে করেন নি, কিংবা তার মধ্যে পথও হারিয়ে ফেলেন নি, বরং এর ওপর তিনি দুঃখোত্তীর্ণ জীবন রসসিক্ত আনন্দ শতদলকে ফুটিয়ে তুলে তার সৌরভকেই ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। দুঃখকে কবি কাব্যের উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন—কারণ জগৎসংসারে সুখ-দুঃখ পাশাপাশি রয়েছে, এর কোনো একটিকে বাদ দিলেই সত্যচিত্ৰ হ’বে অসম্পূর্ণ, যাকে মিথ্যা অপেক্ষাও সাংঘাতিক বলা চ’লে। অতএব কিছু কিছু অভাব-অনটন বা দুঃখ-কষ্টের চিত্র থাকলেও একমাত্র তাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না—কবিও তা চাননি বলেই তাঁকে দুঃখবাদী বা সংশয়বাদী বলা চলে না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা চলে দুঃখদারিদ্র্যের প্রসঙ্গ কাব্যে উত্থাপন করলেই কবি দুঃখবাদী হন না। আমরা তাহার দুঃখজয়ী মনোভাবকে ঠিক গ্রহণ করতে পারিতেছি না। এই দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকারত্ব দুঃখসচেতনতার একান্ত অভাব, দুঃখে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও জীবনরসের উপভোগ—ইহাই ইতিহাসের যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া বাঙালী নিম্নতর সমাজের বৈশিষ্ট্য ও টিকিয়া থাকিবার রহস্য।”
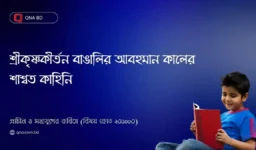
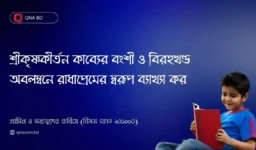
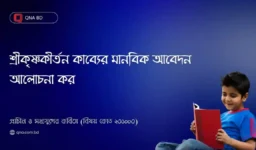
Leave a comment