উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব মুসলিম লেখকগণ বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করে আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মীর মশাররফ হোসেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান গদ্যলেখক। তাঁর মধ্যে একাধারে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক সত্তার সমাবেশ ঘটেছিল। মীরের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয় ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার পাতায়। এখানে কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা’ রূপে লেখক জীবন শুরু করেন। পরে তিনি আজীবন নেহার’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তার কর্মজীবন ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও পরে দুয়ার এস্টেটে ম্যানেজার পদে অতিবাহিত হয়।
মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম ও কর্মজীবন:
১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২৫৪, কার্তিক ২৮ ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে মীর মশাররফের জন্ম হয়। পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন, মা বিবি দৌলতন্নেসা। মশাররফ পিতার দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। রাজকার্যে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার জন্য এঁরা ‘মীর’ উপাধি লাভ করেন। আসলে এঁদের বংশগত উপাধি ছিল ‘সৈয়দ’।
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মীরের জীবন সংগঠিত হয়। শৈশবে মুন্সী সাহেবের কাছে আরবী শিক্ষার এবং জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা পঠন-পাঠন শিক্ষার সূচনা হয়। বয়সকালে ফারসি ভাষার সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। চৌদ্দ বছর বয়সে কুমারখালি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। প্রচলিত কুসংস্কারের বাধা ছিল। মীরের নিজের ভাষায় : “ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মুখে আসিবে না।… ইংরেজী পড়িলে একরূপ ছোটখাটো শয়তান হয়” (উদ্ধৃত, ‘বিষাদ-সিন্ধু’, ভূমিকা, ‘আমার জীবনী’, পৃষ্ঠা ৮-৯)। কুমারখালি স্কুলে স্বল্পকালীন অবস্থানের পর পদমদী নবাব স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু সংসর্গদোষে পড়াশুনো বেশিদূর এগোয় না। তারপরে ভর্তি হন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। এখানে মাত্র সাত মাসের জন্য তাঁর অবস্থান ঘটে। কিন্তু তার প্রভাব হয় গভীরতর। এখানকার হিন্দুয়ানী চালচলন, হিন্দুয়ানী নামকরণ তাঁকে হিন্দুজীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় পিতৃবন্ধু নবাজীর সাহেবের বাড়িতে স্থানান্তরিত হন। সেখানে নবাজীরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিফ-ঊন্-নিসার সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিবাহ হয় লতিফের বোন আজীজ-ঊন্-নিসার সঙ্গে, যা তাঁর ভবিষ্যত জীবনকে বিষময় করে তোলে। ১২৮০ খ্রীঃ তার দ্বিতীয় বিবাহ হয় কুলসমের সঙ্গে। এই বিবি কুলসমই মশাররূে উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সংযত ও সৃষ্টিশীল করে তোলেন। এই দ্বিতীয়া পত্নী কুলসমকে নিয়েই মীর তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ ‘বিবি কুলসম’ রচনা করেন। কুলসমের মৃত্যুবর্ষে এটি প্রকাশিত হয়। কুলসমের মৃত্যুর দু’বছর পর মীর সাহেব পরলোকগমন করেন।
মীর মশাররফ হোসেনের রচনাসমূহ:
মীর মশারর্ফের রচনাগুলিকে (ক) নাটক, (খ) উপন্যাস, (গ) জীবনী-মূলক রচনা এবং (ঘ) পত্রিকা সম্পাদনা এই কয়টি ভাগে উল্লেখ করা যায়।
প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে : ‘বসন্তকুমারী’ নাটক (১৮৭৩), ‘জমিদার-দর্পণ’ (১৮৭৩), ‘এর উপায় কি’ (১৮৭৫) প্রহসন।
দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে : ‘রত্নাবতী’ (১৮৬৯), ‘বিষাদসিন্ধু’ (প্রথম খণ্ড ১৮৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৭, তৃতীয় খণ্ড ১৮৯১), ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৮৯০), ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ (১৮৯৯)।
তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে—‘গোরাই ব্রীজ’ বা গৌরী সেতু (১৮৭৩) নামক কবিতা, ‘সঙ্গীতলহরী’ (১৮৮৭), ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ (১৮৮৯), ‘গো-জীবন’ (১৮৮৯), ‘গো রক্ষার জন্য প্রস্তাব’, ‘হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ’ (১৯০৫), ‘মদিনার গৌরব’ (১৯০৬), মোস্লেম বীরত্ব (১৯০৭), ‘মোস্লেম ভারত’ (১৯০৭), ‘আমার জীবন’ (১৯০৮), ‘এসলামের জয়’ (১৯০৮) গদ্যরচনা ও বিবি কুলসম বা আমার জীবনীর জীবনী’ (১৯১০) প্রভৃতি।
চতুর্থ কাজ আজীবন জেহাব’ (১৮৭৪) নামে পত্রিকা সম্পাদনা। এই পত্রিকার আদর্শ ছিল “হিন্দী-পারসী কলঙ্কিত আদালতী বাঙ্গালার’ পরিবর্তে ‘মধুময় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ স্বাদ’-এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ঘটানো।
মীর সাহেবের রচিত নাটকগুলির মধ্যে রচনাশক্তির উৎকৃষ্টতা যেমন দেখা যায়, তেমনি তার সমাজ-সচেতনতার স্বাক্ষর আছে, বিশেষত ‘জমিদার দর্পণ’ রচনায়। ‘নীলদর্পণ” এই গ্রন্থের পূর্বপ্রেরণা সন্দেহ নেই। তবু বাংলাদেশে প্রজাসাধারণের উপর জমিদারের অত্যাচারের এমন বাস্তব ও দুঃসাহসী চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। নাট্যকারের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের গুণেও গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
‘জমিদারের-দর্পণে’ নাট্যকারের মূল লক্ষ্য, প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার, শোষিতের উপর শোষকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের চিত্রাঙ্কন। নাটকের প্রস্তাবনায় আছে এই দুঃসাহসিক চিত্রাঙ্কনের প্রতিশ্রুতি : “সূত্রধার—’ (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের, কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শাস্ত—বড় ধীর, বড় নম্র হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না! বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে”
বস্তুত, জমিদারদের মাত্রাতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি এবং ইচ্ছেমত প্রজা-উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পাবনা এবং বগুড়ায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে। প্রায় ছয় বছর ধরে তা অব্যাহত থাকে। বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে মীর সাহেবের ‘জমিদার দর্পণে’র চরিত্রেরা তারই কায়ারূপ লাভ করে। এই গ্রন্থটির ভাষারীতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করেছিল: “জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালা অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।” কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গ্রন্থের বৈপ্লবিক সমস্যার অবতারণা ‘সাহিত্যসম্রাটে’র সমর্থন পায় নিঃ “…আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এসময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য” (উদ্ধৃত, ‘বিষাদ-সিন্ধু’, পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ১৮)। এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সামত্ততন্ত্রের প্রতি সমর্থন প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ‘নীলদর্পণে’র প্রকাশকেও প্রথমে সমর্থন করতে পারেন নি।
মীর মশাররফ হোসেনের নীলদর্পণ ও জমিদার দর্পণ:
১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হয় ‘নীলদর্পণে’। এই ধারায় পরবর্তীকালে বেশ কিছু নাটক লেখা হয়; যেমন—জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের সাক্ষাৎ দর্পণ’ (১৯৭১) ধরা পড়েছে বাঙালী সমাজের কদাচার, প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ‘পল্লীগ্রাম দর্পণ’ (১৮৭৩), যোগেন্দ্র ঘোষের ‘কেরাণীর দর্পণে’ (১৮৭৪) ফুটে উঠে কেরাণী সমাজের চিত্র। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘চা-কর দর্পণে’ চা-বাগানের কুলীদের উপর নির্যাতনের ছবি, উৎপীড়িত জেল কয়েদীদের চিত্র প্রকাশিত হয় ‘জেল দর্পণে’ (১৮৭৫)। তবু বলা যায়, এই দর্পণালেখ্য-সাহিত্যধারায় ‘নীলদর্পণ’ অদ্বিতীয় হলেও ‘জমিদার দর্পণের স্থান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।
‘নীলদর্পণ’ এবং ‘জমিদার দর্পণে’ কিছু সাদৃশ্য আছে যেমন, তেমনি পার্থক্যও কম নয়। ‘নীলদর্পণে’ পদী ময়রাণীর মতো ‘জমিদার দর্পণে’ও আছে কৃষ্ণমণি নামে বৈষ্ণবী কুট্টনী নারী। আবার রোগের দ্বারা যেমন ক্ষেত্রমণি ধর্ষিতা হয়েছে, তেমনি হায়ওয়ানের (যার মুসলিম অর্থ ‘পশু’) কামপ্রবৃত্তির বলি হয়েছে নুরুন্নেহার নামে কৃষক রমণী (আবু মোল্লার স্ত্রী)। নবীনমাধব এবং আবু মোল্লার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণাভোগের দিক থেকে কিছুটা নৈকট্য আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য সামগ্রিক নয়। কারণ, ‘নীলদর্পণে’ ক্ষেত্রমণির যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাহাকার ‘জমিদার দর্পণে’ নুরুন্নেহার ক্ষীণ কণ্ঠে উপস্থাপিত। আবার নবীন মাধবের দীর্ঘতর ভাষণ অপেক্ষা আবু মোল্লার সংযত কথাবার্তা অনেক বেশি বেদনাবহ। ‘নীলদর্পণের’ সংলাপের আড়ষ্টতা ‘জমিদার দর্পণে’ নেই। এখানে ভদ্র এবং কৃষক চরিত্রের মুখে গতিময় সংলাপ দেখা যায়। কিন্তু জজ-ডাক্তারের কথাবার্তা বা মোসাহেবদের সংলাপের স্থূলতা ও গ্রাম্যতা ‘নীলদর্পণে’ অনেক কম। এই দুই নাটকে নাট্যকারদ্বয়ের মনোভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। ‘নীলদর্পণে’ অত্যাচারের সার্বিক চিত্রণের সঙ্গে প্রতিবাদের কণ্ঠও সোচ্চার–তোরাপ যার নিখুঁত নিদর্শন। কিন্তু ‘জমিদার দর্পণে’ অত্যাচার নিপীড়নের চিত্র থাকলেও কোথাও কোন বজ্রমস্থ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নেই। নাট্যকারের নৈরাশ্যময় মনোভঙ্গীর প্রকাশ নাট্য সমস্যার সমাধান নির্দেশে সাহায্য করে না। এই নাটকে আরও কিছু ত্রুটি দেখা যায়; যেমন— (ক) নট-নটী-সূত্রধরের দ্বারা নাটক সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে প্রাচীন রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যাত্রাসুলভ আবেগধর্মিতারও প্রকাশ ঘটেছে। (খ) মননরীতির প্রকাশ নাটকের সংলাপে বা উপস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায় না।
মীর মশাররফ হোসেনের প্রবন্ধগ্রন্থ:
‘গো-জীবন’ প্রবন্ধের মধ্যে লেখক মুসলমান হয়েও এমন দুঃসাহসিক অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যা বিস্ময়কর এবং সংবেদনশীলতার পরিচায়ক : “আমি মোসলমান—গো জাতির পরম শত্রু। আমি গো মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি, ধর্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিশোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছ, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি তাহা কোথায় ঢাকিব? …আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক। … ধর্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নাও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধ হয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা ধর্মরক্ষা আর যাহা রক্ষা তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয়, সে ত্যাগে ক্ষতি কি?” সমকালেই ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় এ প্রবন্ধের প্রশংসা করে লেখককে সাধুবাদ জানানো হয়।
মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাসগ্রন্থ:
মশাররফের লেখা উপন্যাসগুলি সমকালেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি “মহরমের উপন্যাস ইতিহাস” বিষাদসিন্ধু’র কাহিনী “পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ” নিয়ে লেখা। ইসলামী রচনা ‘জঙ্গনামা’ এর উৎসস্থল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উপন্যাস লেখার প্রয়োজনে কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ কাহিনীর তিনি কিছু রদবদল করেছিলেন। সুখ-দুঃখে পূর্ণ মানবজীবনের । পরিণাম এই উপন্যাসে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও ট্র্যাজেডির গভীরতায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। একে কেউ বলেছেন ‘ধর্মীয় গ্রন্থ’, কেউ বলেছেন ‘ঐতিহাসিক গ্রন্থ’। কারণ ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিহাস-তথ্য অবলম্বনে এটি রচিত। হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধ, হোসেনের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে পাঠানো, হোসেন পরিবারের অমানুষিক জলকষ্ট ভোগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক। কিন্তু হোসেনের ছিন্ন শির থেকে প্রবাহিত রক্তধারায় এজিদের পরিণাম আরবী অক্ষরে লিখিত হওয়া, ঊর্ধাকাশ থেকে পড়া স্বর্গীয় জ্যোতির আকর্ষণে খণ্ডিত শিরের উপরে উঠে যাওয়া, পূর্বোঘোষিত ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী কারবালার প্রাপ্তরের আকাশে-বাতাসে-বৃক্ষে-মাটিতে আশু মরণ সম্ভাবনার সহস্র ছায়াপাত ঘটা, ফোরাত নদীতে ভাসমান অবস্থায় দুই ছিন্নশির প্রভুভক্ত পুত্রের খণ্ডিত দেহের কাছে পাত্রসহ মস্তক ধরতেই দেহ অনুযায়ী সঠিক যোগাযোগ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাসমূহ অলৌকিকতায় আছন্ন হয়েছে। আসলে ‘বিষাদসিন্ধু’ ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। ঐতিহাসিক কিছু উপাদানের সঙ্গে এখানে মিশেছে মীরসাহেবের জীবনমুখী সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং ঔপন্যাসিকের শিল্পচেতনা। এর প্রতিটি পর্ব এবং প্রবাহে রোমান্সের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেখা দিয়েছে ঘটনাবহুল নাটকীয়তা।
এই উপন্যাসটি অসংখ্য চরিত্রের মিলনভূমি। হাসান, হোসেন, মারওয়ান, গাজী রহমান, হানিফা, হাসনেবাবু, জায়েদা, জয়নাব, কাসেম, সানিকা, আসগর ইত্যাদি। তবু এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে এজিদ। এজিদের লোভ-লালসা ইচ্ছা-অনিচ্ছা উত্থান পতনের সঙ্গে ‘বিষাদসিন্ধু’ উপন্যাসটির কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। এজিদ কুশলী সুনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ, কিন্তু কামনা-লালসা প্রতিরোধে অক্ষম পুরুষ। জয়নাবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দেখা গেছে চিত্তচাঞ্চল্য এবং প্রণয়-ব্যাকুলতা। তার প্রণয়-বিক্ষত আত্মপীড়ন ও দহন অবক্ষয়ের মধ্যে মহাকাব্যের নায়কের ট্র্যাজেডির সুর অনুরণিত হয়েছেঃ “..কে না জানিল যে দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে উৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুইটি চক্ষুই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। …এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ?” হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা চরিত্রাঙ্কনেও মীর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এর ভাষা ফার্সী-বহুল নয়, তৎসম শব্দ-বহুল, গীতিময় উচ্ছ্বাস ও বেদনা, নাটকীয় সংলাপের গীতিময়তায় প্রাণবন্ত; যেমন— “রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্ৰস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে–হায়! খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার, এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? হোসেনের শির তোমার বর্ণাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন? যাইতেছই বা কোথায়? সীমার, একটু দাঁড়াও, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে! একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? কর্তিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? অর্থ, হায়রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি ?”
এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগোচ্ছ্বাস হয়ত অনুভব করা যায়। তবু এই ভাষার প্রত্যক্ষ দৃশ্যময়তা বা চিত্রগুণ, ছোট ছোট বাক্যবন্ধনে আবেগের গতি বিস্তার যে কোন সুরসিক পাঠককেই মুগ্ধ করে। সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন : “বিষাদসিন্ধু আমাকে বিচলিত করিয়াছিল।…সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।”
হোসেন সাহেবের অন্য উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ কৌতুককর কাহিনী। এই গ্রন্থের সমাজচিত্র সর্বস্তরের পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।
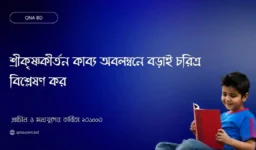
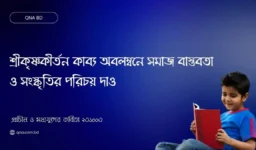
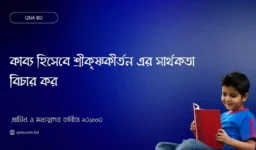
Leave a comment