ভূমিকা: বাংলা সাহিত্যে নাটকের সৃষ্টি ইংরেজি সাহিত্য ও সভ্যতা প্রভাবে। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালি সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকেই পাশ্চাত্য ভাব ও সভ্যতার সাথে বাঙালি নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে থাকে। কলকাতার ইংরেজ সাহেবরা তখন আনন্দবিধানের জন্য নাচ, গান এবং রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ‘প্লে’র আয়োজন করে। ইংরেজদের এই আয়োজন কলকাতা ধনী বাঙালিদেরকে নিজেদের ঘরে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা দান করে। বাঙালির নাট্যপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক আগে থেকেই। মধ্যযুগের বহুকাব্যে নাট্যধর্মিতা প্রত্যক্ষ গোচর। এছাড়া পাঁচালি, কথকতা ইত্যাদি ও সংলাপধর্মী রচনা অনেক সময় অভিনয়ের মাধ্যমে প্রচার করা হতো। লোকনাট্য বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিত। কিন্তু এসব রচনার মধ্যে আধুনিক নাটকের কোনো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল না। ১৭৫৩ সালে ইংরেজরা কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে। ১৭৯৫ সালে রুশ দেশীয় হেরোসিম লেবেডভ ‘বেঙ্গল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করে The Disguise এবং Love is the best Doctor নামে দুটি ইংরেজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের মাধ্যমে নাটকের সূত্রপাত এবং ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাট্য সাহিত্য এদেশে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।
রামনারায়ণ তর্করত্ন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধুর পূর্বযুগের নাট্যকার হিসেবে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তৎকালে ‘নাটুকে রামনারায়ণ’ নামে পরিচিত ছিলেন। সুপণ্ডিত রামনারায়ণ অনেকগুলো নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলোকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:
- সামাজিক নাটক- কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৫)।
- অনুবাদমূলক নাটক- বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭)।
- পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক- রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫) ও ধর্মবিজয় (১৮৭৫)।
- প্রহসন- যেমন কর্ম তেমন ফল (১২৭৯ ব.) উভয় সংকট (১৮৬৯), চক্ষুদান (১৮৬৯) প্রভৃতি।
- রোমান্টিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত- স্বপ্নধন (১৮৭৩)।
এছাড়াও সে সময়ের অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে অনেক নাটক রচনা করান। কালীপ্রসন্ন সিংহ লেখান ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৪)। বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চের জন্য লেখেন ‘রত্নাবলী’। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখান ‘নবনাটক’। পাথুরিয়াঘাটায় অভিনয়ের জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লেখান ‘বিদ্যাসুন্দর’ ও ‘মালতীমাধব’। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে লেখার জন্য তৎকালীন রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। রামনারায়ণ ‘পতিব্রতোপাখ্যান’ (১৮৫২) নাটক রচনা করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।
রামনারায়ণ তর্করত্ন অনেকগুলো নাটক রচনা করলেও ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক দিয়েই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটকের নামকরণ থেকেই এর কাহিনির উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এক কুলীন বৃদ্ধ তার চার কন্যাকে ষাট বছরের এক পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে তার কুলধর্ম রক্ষা করেন। কুলিনের এই চার কন্যার দুঃখ ও বেদনার কথাই বর্ণিত হয়েছে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে। নাটকের কাহিনি অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক। নাট্যকার অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে চার কন্যার বেদনা উপস্থাপন করে সমাজের এই নিষ্ঠুর দিকটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ প্রথম নাটক যা অসাধারণ অভিনয় সাফল্য লাভ করেছিল। নাটকের কাহিনি ও চরিত্র এমন কিছু প্রশংসারযোগ্য নয়; কিন্তু সাধারণ লোকের চরিত্র, ভাষা ও ভঙ্গিমায় তর্করত্ন যে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও বাস্তবতার আমদানি করেছিলেন যার ফলে এই নাটক সে যুগে বহুবার অভিনীত হয়েছিল।
মধুসূদনের পূর্বে তিনিই একমাত্র নাট্যকার যিনি শুধু অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ নাটক রচনা করেছিলেন এবং বেশ সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাবের ফলে রামনারায়ণ তর্করত্নের পুরাতন রীতির নাট্যাভিনয় ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। তবু তিনি অভিনয়কে জনপ্রিয় করার জন্য যে কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন তা অত্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল। আর এজন্যই তিনি এদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
দীনবন্ধু মিত্র: মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক যুগের প্রথম কবি এবং তাঁর রচনায় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও দেশজ ভাষারীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ভাষা প্রয়োগের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখা যায়। দীনবন্ধুর নাটকেও ঈশ্বর গুপ্তের সেই ভাষারীতি অনেকক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। এছাড়া মধুসূদন দত্তের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনটি দ্বারা দীনবন্ধু মিত্র বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কখনো রূপকথা, ইংরেজি বা সংস্কৃত থেকে তিনি তাঁর নাটক রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহারের ভঙ্গিটি দীনবন্ধুর নিজস্ব। চরিত্র এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি সহজেই বাস্তবতার বাতাবরণ নির্মাণ করতে পারতেন। অনেকক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও বিভিন্ন চরিত্র অবিকল তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন।
দীনবন্ধু রচিত নাটকগুলো হলো- ‘নীল দর্পণ’ (১৮৬০), ‘নবীন তপস্বিনী’ (১৮৬৩), ‘বিয়েপাগলা বুড়ো’ (১৮৬৬), ‘সাধবার একাদশী’ (১৮৬৬), ‘লীলাবতী’ (১৮৬৭), ‘জামাই বারিক’ (১৮৭২), ‘কমলে কামিনী’ (১৮৮৩) ইত্যাদি।
দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যক্ষেত্রে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা ‘নীলদর্পণ’ নাটক রচনার মাধ্যমে। বাংলার কৃষকদের উপর ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ নাটকে। সিপাহিবিদ্রোহের পর নীল চাষের উপর
নীলকরেরা নানাভাবে পীড়ন চালাত। ধানের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করে চাষিদের অন্ন উৎপাদনের পথ বন্ধ করে দেয়। দাদন নিতে বাধ্য করে তারা চাষিদের চিরস্থায়ী ঋণের জালে জড়িয়ে পুরুষানুক্রমে শাসন করতো পথ নান্ধ যারে
অনিচ্ছুক চাষিদের জোর করে আটক রাখা, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এমনকি মহিলাদের উপরও অত্যাচার করতে দ্বিধা করতো না। নীলকরদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন গড়ে উঠে, কলকাতার
শিক্ষিত সমাজও কৃষকদের এই আন্দোলনে যোগদান করে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডেও এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে ধীরে ধীরে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং বাংলার কৃষককুল বহুদিনের অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায়।
‘নীলদর্পণ’ নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে গোলকচন্দ্র বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করে। তার পরিবার পরিজন এবং প্রজাবৃন্দ এই নাটকের প্রধান চরিত্র। কৃষকদের উপর অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নীবন বসু ও গোলক বসুকে বিপন্ন হতে হয়েছে। গোলক বসুর আত্মহত্যা, নবীনমাধব এবং সরলার মৃত্যু, সাবিত্রীর উন্মাদ দশা এবং মৃত্যু প্রভৃতি শোচনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হয়েছে।
মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনের অনুরূপ কাহিনি অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন ‘সধবার একাদশী’। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনা প্রহসনের পরিহাস রসিকতার স্তর অতিক্রম করে নাটকের পর্যায়ে উন্নীত। নিমচাঁদকে কখনো প্রহসনের চরিত্র মনে হয় না, বরং মনে হয় শিক্ষাদীক্ষায় পরিমার্জিত, জীবনের শুভাশুভ বিষয়ে প্রখর চেতনাসম্পন্ন একজন মানুষ। নিমচাঁদ চরিত্রের জন্যই ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের সীমা অতিক্রম করে গভীর রসাত্মক নাটকে পরিণত হয়েছে।
‘নবীন তপস্বিনী’, ‘বিয়েপাগলা বুড়ো’ এবং ‘লীলাবতী’ নাটকে প্রেম কাহিনি রচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু ব্যর্থ হলেও কৌতুকরস সৃষ্টিতে যথেষ্ট সফল হয়েছেন। নাটক তিনটি সামগ্রিকভাবে সফল রচনা না হলেও ‘নবীন তপস্বিনী’র জলধর, এবং ‘লীলাবতী’র নদেরচাঁদ হেমচাঁদ প্রভৃতি চরিত্র দীনবন্ধু মিত্রের অসাধারণ সৃষ্টি। বিয়েবাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজিবের বিড়ম্বনা ‘বিয়েপাগলা বুড়ো’র কয়েকটি কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। ‘জামাই বারিক’- এ ঘরজামাইয়ের দল যে বিচিত্র জীবন নির্বাহ করতো তারই হাস্যরসাত্মক চিত্র ফুটে উঠেছে।
পরিশেষে বলা যায় দীনবন্ধুর নাটকে যথেষ্ট অভিনয় উপযোগিতা থাকায় তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন নাট্যশালায় অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে সময়ে প্রহসন জাতীয় নাটক বিশেষ সমাদৃত হতো। দীনবন্ধু এ ধরনের রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশে যা দেখেছেন তাই হাস্যরসের মাধমে নাটকে তুলে ধরেছেন। আর এ কারণেই দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্য সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উপরের লেখায় কোন ভুল থাকে তাহলে দয়া করে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা সেটা ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ধন্যবাদ।
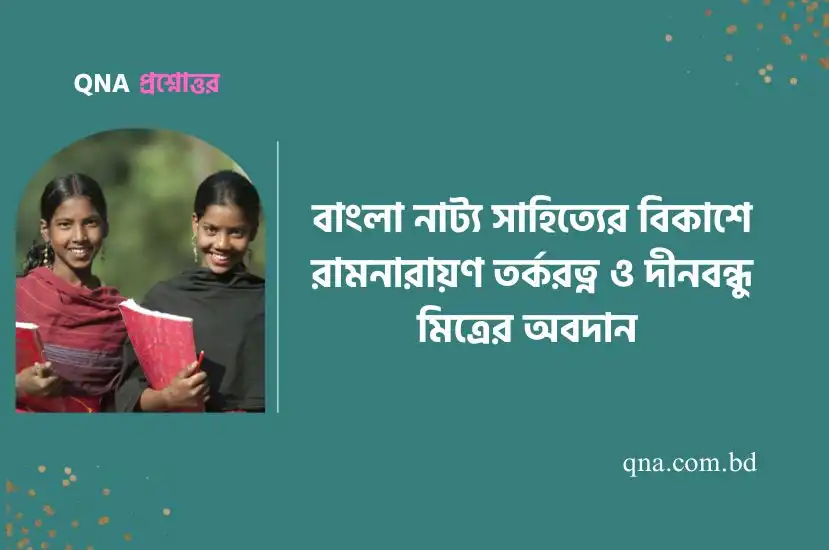



Leave a comment