অথবা, চর্যাপদ যে সময়ে রচিত হয়েছিল সে সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় দাও
উত্তর: চর্যাগীতিকাগুলো বৌদ্ধ সহজিয়াদের পদ্ধতিমূলক গান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্ধ্যাভাষায় রূপকের মাধ্যমে সাধকদের গূঢ় ধর্মসাধনার কথা প্রচার করা। চর্যাপদগুলোর রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে নির্ণীত না হলেও নানা আলোচনা হতে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাতে জানা যায়- এগুলো দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক মতে, এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে পাল রাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল। এ সময় চর্যাপদকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থায় নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থারও চিত্র তুলে ধরেছেন।
চর্যাপদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়- অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয়ে দেখি দুই শ্রেণির মানুষ সমাজে বর্তমান ছিল- দরিদ্র শ্রেণি ও ধনিক শ্রেণি। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ঘর তাদের পড়ে যেত। হাঁড়ি তাদের শূন্য থাকত। এমন অর্থ বঞ্চিত একটি পরিবারের কথা। যেমন-
“টলত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীর ভাত নাহি নিতি আবেসী।” [৩৩ নং পদ]
এসব মানুষ বিচিত্র পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের কেউ মদ বিক্রি করে (৩), কেউ মাঝি বৃত্তি করে (১৪) কেউ বাঁশের চাঁঙ্গারী বিক্রি করে (১০), কেউ তাঁত বুনে (১৭), কেউ শিকার করে (৬,২৩) তাদের সংসার চালাত। সব মিলিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। আবার একদল মানুষের অবস্থা ছিল যথেষ্ট ভালো। তারা ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণির। বজরা নৌকায় পাটি (৪৯) সাজিয়ে তারা বাণিজ্যে যাত্রা করতো। সোনা রুপায় ভরা থাকত (৮) তাদের নৌকা। -এ চিত্র সমৃদ্ধ বাংলার।
১. উৎসব-অনুষ্ঠানের চিত্র: চর্যাপদের মানুষজন আনন্দ উৎসবেও মেতে উঠত। বিবাহ, শিকার ইত্যাদি অনুষ্ঠান ছাড়াও নাচ- গান নাটকাদিও তারা অভিনয় করতেন। ১৯নং চর্যায় পাই ডোম্বী বিবাহের চিত্র। এই বিবাহ সাধারণ বিবাহ থেকে ভিন্ন নয়। বর দোলায় চড়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিয়ে করতে যায়। পাটই মাদল দুনাভী-উলু জোকারে জয় জয় শব্দ উত্থিত হয়।
২. বিয়েতে বর কৌতুক লাভ করে: হরিণ শিকার (৬,২৩), দাবা খেলা (৯) প্রভৃতি ছিল তাদের ক্রীড়া কৌতুকের অঙ্গ। আনন্দে উৎসবে তারা নাচ-গান করতো। ডোম রমণীদের নৃত্য কুশলতা দর্শকের মনোরঞ্জন করতো। পদ্ম দলে, ডোম্বীর নাচ (১০) ছিল আকর্ষণীয়।
৩. প্রেম-দাম্পত্যের পরিচয়: সমাজে চিত্রের আলোচনায় নারী পুরুষের প্রেম-সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চর্যাপদের সমাজ ছিল রক্ষণশীল। উঁচু জাতির ব্রাহ্মণ নীচ রমণীর সঙ্গ করতো :
“নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাসি বামহণ নাড়িআ ॥” [১০ নং চর্যা]
নারী চায় গৃহমুখী স্বামী ও ঘরমুখী সন্তান। কিন্তু তা স্বামী ছিল বেকার ও উদাসীন। নারী তখন গভীর দুঃখে বলে- ‘হাঁউ নিরাসী ক্ষমা সাঙ্গ” শ্লেষ ঝরে কণ্ঠে: নব যৌবন মোর ডইলোসী সুরা (২০)। তাই সে অভিসারিকা। দিনের বেলায় যে নিজের ছায়া দেখলে ভয় পায়, রাতে শ্বশুর ঘুমালে সেই অভিসারে বেরোয় (২০)। সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিল।
৪. ভৌগোলিক চিত্র: মাসদের প্রাপ্ত চিত্র থেকে নদীমাতৃক বাংলার পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নৌচালনা, সাঁকো নির্মাণ, কর্দমাক্ত রাস্তার (৫) কথা পাওয়া যায়- যেমন, তেমনি পর্বত (২৮) ও অরণ্য ঘেরা (৬,২৮) এবং ভূমির কথা ও চর্যাপদে লিপিকৃত। ৮ ও ৪৯ নং চর্যায় নদীমাতৃক বাংলার চিত্র আমাদের নজর কাড়ে। তাছাড়াও বিভিন্ন পদে প্রাপ্ত হাড়ি, কড়া, গাড়, কুঠাল, খন্তা প্রভৃতি নিজ ব্যবহার্য জিনিস থেকে সে যুগের সমাজ চিত্রের পরিচয়টিকেও চিনে নেওয়া যায়।
৫. পেশাগত চিত্র: চর্যাপদে যাদের চিত্র পাওয়া যায় তারা ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বিপর্যন্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, নদী, নৌকা, সাঁকো, ঘাট, পাটনী, মূষিক, তুলো, সোনা-রুপা, মদ, অবৈধ প্রেমকাহিনি, প্রতিবেশ, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব নির্জিত মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। শবর মেয়েরা খোঁপায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জরের মালা পরতো। চর্যাপদে কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, চণ্ডালী, ব্যাধ, শবরী, তাঁতি, ধুনুরী, গুঁড়ি, মাহুত, নট-নটী, পতিতা নানান শ্রেণির কথা চর্যাপদে উঠে এসেছে। কয়েকটি চর্যায় ব্যাধ বৃত্তির কথাও বলা হয়েছে।ব্যাধকর্তৃক হরিণ শিকারের দৃশ্য ফুটে উঠেছে ৬ নং চর্যায়। যেমন-
” কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ না ছাড়ই ভুসুক অহেরী ॥”
পরিশেষে বলা যায়, সব মিলিয়ে চর্যাপদে যে মানব সমাজের পরিচয় আছে তা এক সময়ের বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার দলিল হিসাবে বাঙালির অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।
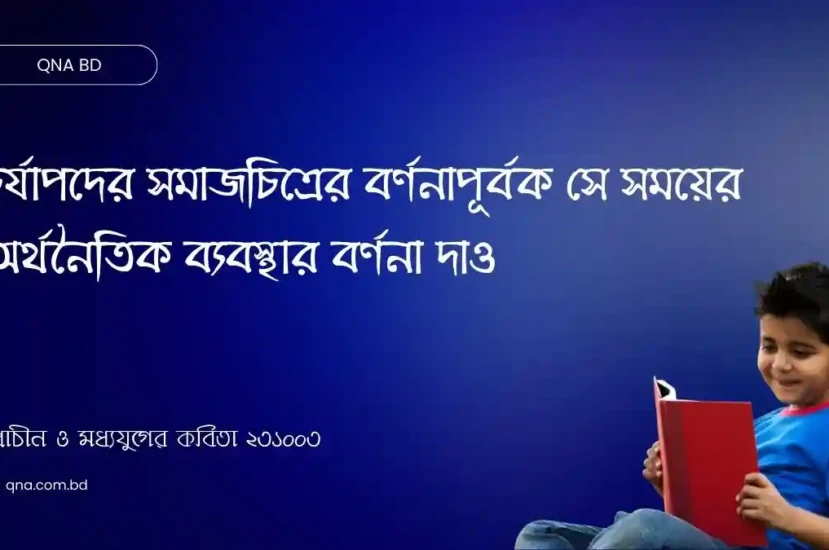
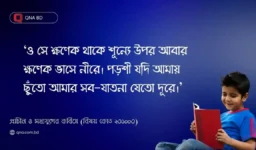
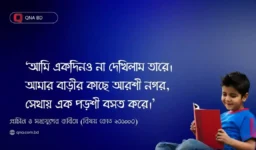
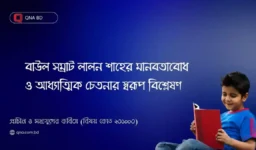
Leave a comment