উনিশ শতকের আগে থেকেই বাংলা লেখ্য গদ্যের যে রূপ প্রচলিত ছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেই রূপটি অবলম্বন করেই বাংলা গদ্যের তথা বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।
১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তারপর থেকেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মুনশি এবং বাংলা-জানা বিদেশি পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যে বই লিখতে শুরু করেন। তাঁদের হাতে, বিশেষ করে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে বাংলা লেখ্য গদ্য এক নতুন কলেবর ধারণ করে। নতুন উদ্ভাবিত কোনাে ভাষা নয়, প্রচলিত গদ্যভাষার কাঠামােকে অবলম্বন করে এবং প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এই পণ্ডিতবর্গ বাংলা লেখ্য গদ্যের বহিরঙ্গে অনেক পরিবর্তন আনেন। তাঁরা দীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ক্রিয়াপদ এবং সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা একটা নিয়ম গড়ে তােলেন। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যিক গদ্য বা লেখ্য গদ্যের যে রূপ গড়ে ওঠে তা অতিমাত্রায় সংস্কৃত-প্রভাবিত। তবে মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতের এই প্রভাব মূলত শব্দচয়ন ও প্রয়ােগের ক্ষেত্রে, অন্বয়ের ক্ষেত্রে নয়।
উনিশ শতকের গােড়ায় সংস্কৃত-প্রভাবিত এই গদ্যশৈলী ‘সাধু গৌড়ীয় ভাষা’ বা ‘সাধু ভাষা’ নামে পরিচিত হয়। প্রথম দিকে সাধুভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা তাে ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল আড়ষ্ট, কখনাে কখনাে পাঠকের কাছে বেশ পীড়াদায়কও। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ভাষাই ধীরে ধীরে সাবলীল ও শিল্পগুণ-সমন্বিত হয়ে উঠতে থাকে।
১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামে একটি বই লেখেন। বইটি কথ্যরীতিকে আশ্রয় করে লেখা। এতে মৌখিক বাচনভঙ্গির অবিকল প্রতিরূপ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইজন্য অনেকে বইটিকে চলিতভাষায় রচিত বলে মনে করেন। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল-কে খাঁটি চলিতভাষায় লেখা বই বলা চলে না। এর মধ্যে সাধুভাষা, কথ্যভাষা মিলেমিশে এক হয়ে আছে। ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এর কয়েক বছর পরে (১৮৬২ খ্রি.) প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা ‘হুতােম প্যাচার নকশা’। এই বইটিই মােটামুটি চলিতভাষায় লেখা একটি বই। সাধুভাষা-প্রভাবিত বাংলা গদ্যের একাধিপত্যের যুগে ‘হুতোম পাচার নক্শা’র প্রকাশ বিস্ময়কর। তবে এই বইয়ের ভাষা কোনাে কোনাে ক্ষেত্রে রুচির সীমা অতিক্রম করে গেছে।
উন্নতমানের সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে চলিতভাযাকে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর য়ুরােপ-প্রবাসীর পত্র’ নামক চলিতভাষায় লেখা বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। বিবেকানন্দের পরিব্রাজক গ্রন্থেও চলিত ভাষার প্রয়ােগ লক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে চলিতভাষা ব্যবহারের ব্যাপক উদ্যোগ দেখা দেয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকা প্রকাশের পরে। এরপরে সাহিত্যের অঙ্গনে যে ভাষা উপেক্ষিত ছিল তাকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করতে লাগলেন বিভিন্ন লেখক।
বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক উপভাষা সাধুভাষা ও চলিত ভাষা —এই দুটি ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাষার পার্থক্যগুলি এরকম-
-
সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চলিতভাষায় ব্যবহৃত হয় সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন করিতেছি > করছি, যাইতেছি > যাচ্ছি, করিয়াছিলাম > করেছিলাম ইত্যাদি।
-
সাধুভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ইহারা, তাহারা, তাহাদিগকে, যাহা, তাহা, উহাকে, তাহাদের ইত্যাদি। চলিতভাষায় ব্যবহৃত হয় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন—এরা, তারা, যা, তা ইত্যাদি।
-
উভয় রীতিতে অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধু ভাষার হইতে, দ্বারা, দিয়া, চাহিয়া ইত্যাদি চলিতভাষায় হতে বা থেকে, দিয়ে, চেয়ে প্রভৃতি রূপ ধারণ করে
-
সাধুভাষায় সংস্কৃত অব্যয়ের ব্যবহার বেশি। যেমন- অনন্তর, যদ্যপি, তথাপি প্রভৃতি। চলিতভাষায় সংস্কৃত অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন-তারপর, যদিও, তবুও প্রভৃতি।
-
সাধুভাষায় সন্ধি-সমাসের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-বিদ্যুদ্দীপ্তি, মন্দিরাভ্যন্তর, বনান্ধকার প্রভৃতি। চলিতভাষায় এগুলিকে যথাসম্ভব ভেঙে সহজ করে লেখা হয়ে থাকে। যেমন-বিদ্যুতের আলাে, মন্দিরের ভিতর, বনের অন্ধকার প্রভৃতি।
-
সাধুভাষার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে উদ্দেশ্য ও পরে বিধেয় থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ বসে বাক্যের শেষে। কিন্তু চলিতভাষার ক্ষেত্রে পদবিন্যাসের নির্দিষ্ট ক্রম বজায় রাখার কোনাে নিয়ম নেই।
-
চলিতভাষায় স্বরসংগতি এবং অভিশ্রুতির প্রভাব বেশি। যেমন—পূজা > পুজো, উনান > উনুন, করিয়া > কইর্যা > করে ইত্যাদি।
-
চলিতভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বিশিষ্টার্থক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, প্রভৃতির প্রয়ােগ যতটা স্বাভাবিক, সাধুভাষায় ততটা নয়।
কোনাে একটি ভাষার ছােটো ছােটো রূপবৈচিত্র্য নিয়েই তৈরি হয় উপভাষা-শৃঙ্খল। যেমন ‘উপভাষা-১’, ‘উপভাষা-২’, ‘উপভাষা-৩’ ইত্যাদি। এই প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাষার মানুষ যে অন্য সবকটি উপভাষা ভালােভাবে বুঝতে পারে, এমন নয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষ চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বুঝতে পারেন না। দুটোই অবশ্য বাংলা ভাষা।
আবার দেখা যায় যে, ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষ মেদিনীপুর সংলগ্ন ওড়িশা অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য ওড়িয়া ভাষা সহজেই বুঝতে পারেন। এক্ষেত্রে এই দুই ভাষার মধ্যে পারস্পরিক বােধগম্যতা (Mutual Intelligibility) থাকায় আমরা এটা ভেবে প্রলুদ্ধ হই যে, ওই দুটি উপভাষা (একটি বাংলা, অন্যটি ওড়িয়া) একই ভাষার সম্পর্কিত। কিন্তু তা তাে নয়। এখানেই প্রশ্ন, কী করে বােঝা যাবে যে, এদের কোন্টি কোন্ ভাষার উপভাষা? ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুরবাসী পশ্চিমবাংলা-সংলগ্ন কথ্য ওড়িয়া ভাষাটি বুঝতে পারলেও মান্য ওড়িয়া তারা বুঝতে পারে না, অথচ মান্য বাংলা বােঝে। তাই ওই উপভাষাটি বাংলারই উপভাষা, ওড়িয়ার নয়।
একইরকমভাবে চট্টগ্রামের মানুষও ওড়িশা-সংলগ্ন আঞ্চলিক রূপটি বুঝতে না পারলেও মান্য বাংলা বুঝতে পারে, তাই বাংলা ভাষারই উপভাষা হল চট্টগ্রামের ভাষা। এইভাবে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাষার মধ্যে মান্যভাষার বােধগম্যতার দিক দিয়ে একটি শৃঙ্খলা আছে। এই শৃঙ্খলাকেই বলা হয় উপভাষা-শৃঙ্খল।
বাংলাভাষার সামগ্রিক ভাষাবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলােচনা করাে।
ভাষা বলতে কী বােঝ? কোন্ উপভাষা নিয়ে এবং কেন মান্য চলিত বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে?
উপভাষা কাকে বলে? উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী উপভাষাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? প্রতিটি ভাগের আলােচনা করাে।
মান্যভাষার পরিচয় দিয়ে উপভাষার সঙ্গ মান্যভাষার তুলনা করাে।
রাঢ়ি উপভাষার প্রচলিত অঞ্চলগুলি লেখাে। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখাে।
রাঢ়ি উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখাে।
ঝাড়খণ্ডি উপভাষার প্রচলিত অঞ্চলগুলি লেখাে। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখাে।
ভাষা কীভাবে ব্যক্তি, পেশা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলাদা রূপ নেয়, তা দেখাও।
লিঙ্গনির্ভর সমাজভাষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলােচনা করাে।
গ্রাম ও শহরভেদে ভাষার পার্থক্য আলােচনা করাে।
সম্প্রদায়ভেদে ভাষাগত পার্থক্য আলােচনা করাে।
প্রাক-উনিশ শতকের সাধুগদ্যের পরিচয় দাও।
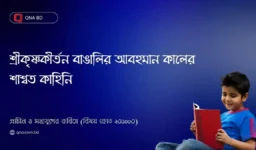
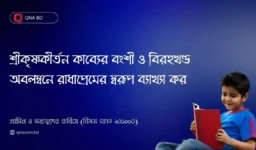
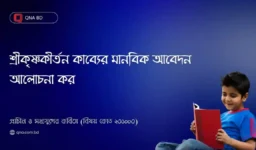
Leave a comment